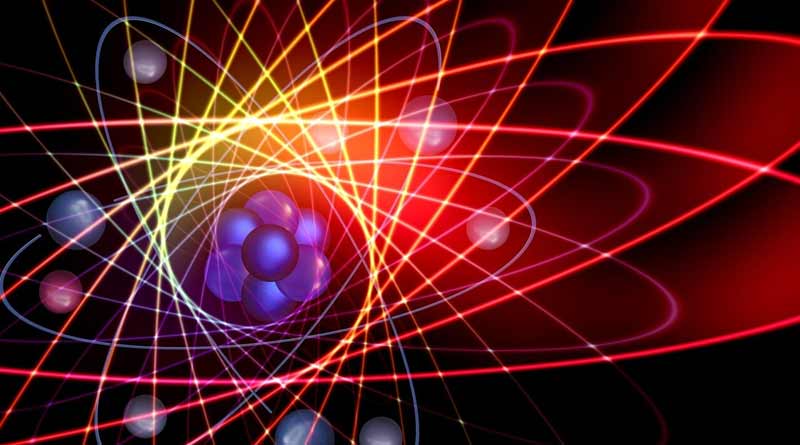
১৯৬৪ সালে যুগান্তকারী গবেষণায় জন বেল বলেন, পরমাণু জগতে যদি ‘গুপ্ত বিবরণ’ (হিডেন ভেরিয়েবল) থাকে, যা গোড়া থেকেই তাদের চরিত্র নির্ধারিত করে দেয়, তাহলে পরিসংখ্যানের দিক থেকে কিছু তফাত দেখা দিতে বাধ্য। এবার পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী আলাঁ আস্পে, জন এফ ক্লাউসার, আন্টন জাইলিঙ্গার সেই বক্তব্যকে হাতেনাতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কলমে বিমান নাথ
তরুণ বিজ্ঞানী আলাঁ আস্পে সাতের দশকে জেনিভায় গিয়েছিলেন জন বেল-এর সঙ্গে দেখা করতে। সেই সময় জন বেলের কাজ বিজ্ঞানী মহলে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। বেলের হিসাবটি পরীক্ষাগারে খতিয়ে দেখা যায় কি না সেই নিয়ে বিশদ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আস্পে গিয়েছিলেন জেনিভায়। বেলের সোজাসাপটা প্রশ্ন: চাকরি পাকাপোক্ত তো? এই কঠিন পরীক্ষার ঝুঁকি নিতে পারবেন? গবেষণার জীবনের প্রথম পরীক্ষাই যদি অসফল হয়, তাহলে!
সেই পরীক্ষা আটের দশকের প্রথম দিকে সফল হয়েছিল তো বটেই, এর জন্য এ বছর নোবেল স্বীকৃতি পেলেন আলাঁ আস্পে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর। নোবেল পুরস্কার পেলেন এবার জন এফ ক্লাউসার-ও। তিনিই ১৯৬৯ সালে (তাঁর ছাত্র স্টুয়ার্ট ফ্রিডম্যানের সঙ্গে) প্রথম পথ দেখিয়েছিলেন কীভাবে বেলের হিসাব হাতেনাতে যাচাই করা যেতে পারে। এবং পরবর্তীতে এই পথ ধরে কোয়ান্টাম কণার দূর-পরিবহণ (টেলিপোর্টেশন) বাস্তবায়িত করার জন্য আন্টন জাইলিঙ্গারকেও পুরস্কৃত করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে জন বেলের মৃত্যু না হলে তাঁকেও নিশ্চয়ই শামিল করা হত এই তালিকায়।
তা কী সেই হিসাব যা নিয়ে এত মাতামাতি? সহজ করে বললে, কোয়ান্টাম জগতের নিয়মগুলো নিয়ে যে-তর্ক, জন বেল সেসব দার্শনিক স্তর থেকে পরীক্ষাগারে নিয়ে আসার উপায় বাতলেছিলেন। পরমাণু জগতের নিয়ম নিয়ে বিজ্ঞানীরা গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে মাথা ঘামিয়ে আসছেন। এক-একটা পরীক্ষার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব নিয়মের কথা তাঁদের ভাবতে হয়েছিল যা আমাদের স্থূল জগতের যৌক্তিকতার বাইরে। ধরুন, কেউ একজন দাবা খেলা দেখছেন, অথচ তিনি খেলার নিয়মকানুন জানেন না। চাইলে তিনি দাবাড়ুদের চাল লক্ষ করে ধীরে-ধীরে দাবার নিয়মগুলো শিখে নিতে পারেন। বিজ্ঞানের কাজটাও এরকম। প্রকৃতির ঘটনা থেকে অন্তর্নিহিত নিয়ম বের করার চেষ্টা করেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু পরমাণু জগতের ব্যাপারগুলো যে নিয়মে চলে সেগুলো মোটেই আমাদের স্থূল বাস্তব জগতের যুক্তির সঙ্গে মেলে না।
যেমন, ধরা যাক, একটি ইলেকট্রন দু’টি ভিন্ন অবস্থায় (স্টেট) থাকতে পারে। কোয়ান্টাম নিয়ম বলে দেয়, পরীক্ষা করে দেখা অবধি সেই ইলেকট্রনের কোনও নির্দিষ্ট অবস্থা থাকে না। দুই সম্ভাব্য অবস্থার মধ্যে একটা দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে থাকে সেটি। দুই অবস্থার এক ধরনের যোগফল আর কী, যাকে বলে ‘সুপারপজিশন’। সিনেমায় দু’টি দৃশ্য ডিজলভ করার মুহূর্তে যেমন দুটো ছবিই আবছা দেখা যায়, তেমন। এটা আমাদের স্থূল জগতের সঙ্গে মেলে না মোটেই। জঙ্গলে একটা গাছ ভেঙে গিয়েছে না দাঁড়িয়ে আছে- সেটা হয়তো না-দেখা পর্যন্ত আমরা জানতে পারি না, কিন্তু আমাদের দেখার আগেও গাছটি ভাঙা অথবা দাঁড়ানো এই দুইয়ের কোনও একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় ছিল এ কথা নিশ্চিত।
পরমাণু জগতের নিয়ম সেরকম নয়। সেখানে দুই অবস্থাতেই বিচরণ করতে পারে পদার্থকণা। সেজন্য কোয়ান্টাম নিয়মে কোনও পরীক্ষার ফলাফল নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। শুধু কী হতে পারে তার সম্ভাবনার একটা হিসাব দেওয়া যায়। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মনে করতেন, এটা কোয়ান্টাম বিদ্যার সীমাবদ্ধতা। তাঁর মতে, কোয়ান্টাম নিয়মের গূঢ় কারণ আমরা এখনও জানি না বলেই এমন সম্ভাবনার আঁক কষতে হচ্ছে। পদার্থকণার ‘অবস্থা’-র বিবরণে খামতি রয়ে গিয়েছে হয়তো। যেমন, বাতাসের তাপমাত্রা বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হল অগুনতি অণুর ছোটাছুটির একটি স্থূল মাপ। এখানে প্রত্যেকটি অণুর চলাফেরার ধরন না জানলেও চলে। সেগুলোর সার্বিক পরিসংখ্যান থেকেই তাপমাত্রার আন্দাজ পাওয়া যায়। একইরকমভাবে, কোয়ান্টাম অবস্থা জানার জন্য হয়তো আরও গভীরের কিছু বিবরণ জানা প্রয়োজন। এই সূত্র ধরে, কোয়ান্টাম নিয়মের অসম্পূর্ণতা বোঝানোর তাগিদে তাঁর ছাত্র পডল্স্কি এবং রোজেনের সঙ্গে লেখা প্রবন্ধে তিনি একটি ধাঁধার কথা তুলে ধরেন। সে ১৯৩৫ সালের কথা।
এর কুড়ি বছর পর ডেভিড বোম ধাঁধাটি একটু বদলে দিয়ে পরিবেশন করলেন। ধরা যাক, দু’টি ইলেকট্রনকে এমন এক অবস্থায় সাজানো হল যাতে তাদের একটি বিশেষ চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিপরীতধর্মী। যেমন, স্পিন। ইলেকট্রনকে চুম্বকের কাছে রাখলে সেটি চুম্বকের হয় উত্তর মেরু নয়তো দক্ষিণ মেরুর দিকে ঘুরে যায়। এটাই তাদের স্পিন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। এবারে এভাবে দুটো ইলেকট্রনকে শুরুতে গাঁটছড়া বেঁধে দিলে তাদের চরিত্র আর পাল্টাবে না। এক-একটিকে বহু দূরে পাঠালেও না। তখন যদি একটি ইলেকট্রনকে ধরে তার স্পিনের দিক জানা যায়, তাহলে বোঝা যায় তার যমজ ইলেকট্রনটির স্পিন উল্টো। হতেই হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তো দ্বিতীয় ইলেকট্রনটিকে পরীক্ষা না করেই জানা গেল তার অবস্থা!
যদি বলা হয়, না, এক্ষেত্রেও সেটা দুই অবস্থায় বিচরণ করছিল, তাহলে বলতে হবে একটি পরীক্ষার ফলের খবর অন্য জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে দ্রুতবেগে। কোনও উপায়ে। সেটা আলোর গতিবেগের চেয়েও দ্রুত হতে হবে। কিন্তু সেটা তো অসম্ভব! অর্থাৎ, হয় ‘সুপারপজিশন’ বলে কিছু নেই, নয়তো মেনে নিতে হবে, কোয়ান্টাম জগতে ‘স্থানীয়’ বলে কিছু হয় না। বাস্তব হতে হবে অস্থানিক, যেখানে এক জায়গার খবর নিমেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে।
কোনও মীমাংসা ছাড়াই এই ধাঁধা নিয়ে দার্শনিক আলোচনা হয়েছে ত্রিশ বছর ধরে। এরপর ১৯৬৪ সালে এক যুগান্তকারী হিসাব কষে দেখালেন জন বেল। তিনি বললেন, পরমাণু জগতে যদি ‘গুপ্ত বিবরণ’ (হিডেন ভেরিয়েবল) থাকে, যা গোড়া থেকেই তাদের চরিত্র নির্ধারিত করে দেয়, তাহলে পরিসংখ্যানের দিক থেকে কিছু তফাত দেখা দিতে বাধ্য। তখন পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে কোয়ান্টাম জগতে সুপারপজিশন আদৌ আছে কি না। জন বেলের এই হিসাব নিয়ে সেই সময় বিজ্ঞানী মহলে তুলকালাম কাণ্ড। কীভাবে হাতেনাতে পরীক্ষা করা যায়, সবার মাথায় ছিল এই প্রশ্ন। হিসাবটা খুব কঠিন না হলেও একেবারে সহজও নয়। তবু একটি উদাহরণের সাহায্যে সেই হিসাবের একটা নমুনা তুলে ধরা যাক।
যেমন, কারও এক পায়ের মোজা দেখলে বোঝা যায় অন্য পায়ের মোজাটি কেমন। যদি মানুষটি তেমন পাগলা গোছের না হয় তাহলে দু’-পায়ে একইরকম মোজা পরবে। ধরা যাক, তিনটে চরিত্র দিয়ে মোজা চেনা যায়। প্রথমত সেটি কী দিয়ে তৈরি (সুতির না নাইলনের), দ্বিতীয়ত এর রং (নীল না লাল), এবং তৃতীয়ত এতে কোনও নকশা আছে কি না (থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে)। অর্থাৎ, প্রতিটি চরিত্রের দুটো করে সম্ভাব্য অবস্থা রয়েছে। দেরাজে মোট ২x২x২= আটটি মোজা রয়েছে। দেরাজ থেকে যে কোনও মোজা বের করে পরার সম্ভাবনা সমান। এবার দিনের পর দিন লক্ষ করে একটা পরিসংখ্যান নেওয়া হল। নীল-সুতির মোজা এবং নাইলনের নকশা-ছাড়া মোজা- এই দুই কিসিমের মোজা পরার মোট দিনের হিসাব করতে হবে। দেখা যাবে, এই যোগফল নীল নকশাওয়ালা মোজা পরার দিনের চেয়ে বেশি। সমীকরণ নয়, এটি একটি অসাম্যের হিসাব। বেলের প্রমাণিত অসাম্যের একটি উদাহরণ। কিন্তু কোয়ান্টাম নিয়মে বিভিন্ন মোজা থাকার কথা নয়- নীল-লাল ইত্যাদি চরিত্রগুলোর মধ্যে বিচরণ করবে মোজাগুলো। শুধু এই ক্ষেত্রে একটি লাল (বা নাইলনের) হলে অন্যটিও লাল (এবং নাইলনের) হতে হবে।
সুপারপজিশনে থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে কোয়ান্টাম নিয়মে মোজার নানা চরিত্রের সঙ্গে একটা সম্পর্ক থাকবে। এখানেই বেলের আসল কেরামতি। কোয়ান্টাম নিয়মের হিসাব কষে বেল দেখিয়েছিলেন এক্ষেত্রে আগের হিসাবটি খাটে না। সেখানে প্রথম দুটো সংখ্যার যোগফল তৃতীয়টির চেয়ে বেশি না হয়ে কম হবে। বেলের এই অসাম্য (‘বেল ইনইকুয়ালিটি’) মানে না কোয়ান্টাম জগৎ।
এক্ষেত্রে মোজা হচ্ছে পরমাণু জগতের কণা। যেমন, ইলেকট্রন। পরীক্ষা করার সময় ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে তিনদিকে চুম্বক রাখা যেতে পারে- উত্তর, অগ্নি (দক্ষিণ-পূর্ব) এবং নৈর্ঋত (দক্ষিণ-পশ্চিম) দিকে। ইলেকট্রনটির স্পিন যদি উত্তর দিকে থাকে, তাহলে প্রথম যন্ত্রের মধ্যে যাওয়ার সময় সেটি একটি সংকেত দেবে। দক্ষিণে থাকলে সেই সংকেত হবে উল্টো। এখানেও তাহলে মোজার তিনটে চরিত্রের দুটো করে সম্ভাবনার মতো ব্যবস্থা করা গেল। আমাদের উদাহরণে দুটো মোজা একইরকমের ছিল, এখানে কণাগুলো উল্টো ধর্মের, তাই বেলের অসাম্যের হিসাবে একটু অদলবদল হবে। আস্পে এই পরীক্ষাটিই করেছিলেন, ইলেকট্রনের বদলে ফোটন, অর্থাৎ আলোর কণা নিয়ে। ক্লাউসারের তুলনায় আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষা ছিল সেটি। কারণ একটি মাত্র ফোটন ধরার ক্ষমতাও ছিল সেখানে। ক্যালসিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রনকে এমনভাবে শক্তি ক্ষয় করে আলোর কণা তৈরি করা হয়েছিল, যাতে দুটো ফোটন বেরয়- বিপরীতধর্মী চরিত্রের। এখানে স্পিনের বদলে আলোর ঢেউয়ের ওঠা-নামার দিক মাপার চেষ্টা করা হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, বেল-অসাম্য মানছে না ফোটনের পরিসংখ্যান। ক্লাউসার এবং আস্পের পরীক্ষা প্রমাণ করে দিল যে যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন, প্রকৃতির নিয়ম অস্বীকার করার উপায় নেই।
আস্পের পরবর্তীতে এই নিয়ে আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। বলা যায়, এসব পরীক্ষা কোয়ান্টাম জগতে আরেকটি বিপ্লব নিয়ে এসেছে একশো বছর পর। গঁাটছড়া বেঁধে কণাগুলোকে এক-এক জায়গায় পাঠালে কণাগুলোর চরিত্র পরীক্ষা করে ‘তথ্য’-ও পাঠানো যাবে। সেক্ষেত্রে কেউ আড়ি পাতলে ধরা পড়ে যাবে, কারণ কোয়ান্টাম নিয়মে কোনও যন্ত্রে একটি কণাকে ধরে তথ্য বার করে নিলে সেটার আভাস পড়বে অন্য কণার ক্ষেত্রেও। এর উপর ভিত্তি করেই তৈরি হচ্ছে কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি। তথ্য সরবরাহের এক নিরাপদ পদ্ধতির খোঁজ চলছে কোয়ান্টাম জগতের অদ্ভুত নিয়ম কাজে লাগিয়েই। ভবিষ্যৎ বলে দেবে এই গবেষণার জল কোথায় গড়ায়।
খবরের টাটকা আপডেট পেতে ডাউনলোড করুন সংবাদ প্রতিদিন অ্যাপ





Copyright © 2025 Sangbad Pratidin Digital Pvt. Ltd. All rights reserved.